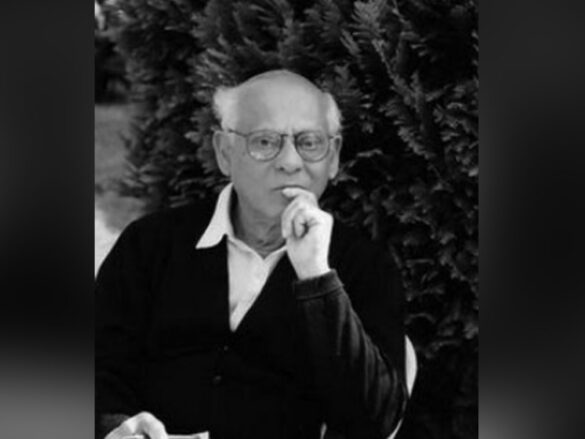হাসিবুর রহমান
আগাথা ক্রিস্টির একটি নাটকের দৃশ্যে সপ্তম শ্রেণীর এক কিশোরী ছাত্রী শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইতিহাসই তার কাছে একমাত্র জঘন্য বিষয় যেখানে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। ভূগোল বা বিজ্ঞানের মত বিষয়ে এমন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সকল অর্থে ব্যাখ্যার বহুমুখী দৃষ্টিকোণ যে ইতিহাস দর্শনের মূল রসায়ন তা কিশোরীর বোধগম্যতার অতীত।
আসলে ইতিহাসে ‘মত ও পথ’ সর্বজনবিদিত। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় বহুমাত্রিক ঘরানার কারনে নতুন নতুন বিষয় ইতিহাসে চিত্রকর্ষক হয়ে উঠেছে। যুক্তিগ্রাহ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত ইতিহাস হয়ে পড়ে তথ্য ও বস্তুগত উপাদানের নিরস বিবরণ মাত্র। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন ছাড়া ইতিহাস চর্চা প্রাণহীন এক নিরন্তর প্রয়াস। সম্রাজ্যবাদী , জাতীয়তাবাদী, মার্কসীয় , উত্তর আধুনিক , কেমব্রিজ , অ্যানাল গোষ্ঠীর মতো সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় নব্য ঘরানার ইতিহাসবিদ্যা চর্চা এখন জনপ্রিয়, যার উদ্ভাবক ছিলেন ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ। তিনি গত শতকের সত্তরের দশকে নিম্নবর্গীয় ভাবনা সমন্বিত ধারনাটি সফলভাবে ইতিহাসপ্রেমী, গবেষক,স্কলার, এমনকি জনসমাজে বিস্তার করতে সক্ষম হন।
নিম্নবর্গীয় বা সাবলটার্ন স্টাডিজের ধারণার উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বলেন, ‘Subaltern’ শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো সামরিক ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের ক্ষেত্রে। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত. . . .ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল ‘সাবর্ডিনেট ‘। মার্কসীয় আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির ( ১৮৯১-১৯৩৭ ) বিখ্যাত কারাগারের নোটবইতে …. সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সাবলটার্ন শ্রেণীর ধারণাটির সফলভাবে উপস্থাপন করেছেন বরেণ্য ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ , তিনিই এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন ‘নিম্নবর্গ’ এখানে ‘নিম্নবর্গ’। বলতে তিনি নিম্নবর্গের মানুষ বা প্রলেতারিয়েত বুঝিয়েছেন। ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য , পদ্ধতি, কর্মসূচির বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন এভাবে। ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে নিম্নবর্গের ভূমিকা নির্ধারণ করা হল নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। অধ্যাপক রণজিৎ গুহর দু’টি প্রবন্ধে ‘এলিমেন্টারি আসপেকটস অব পেজান্ট ইনসারজেনসি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ’ এবং ‘প্রোজ অব কাউন্টার ইনসারজেন্সি’–তে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে।
রণজিৎ গুহ লিখেছেন, আমাদের দেশে আধুনিক কালে ইতিহাসবিদ্যার জন্ম ইংরেজ রাজ শক্তির ঔরসে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তা ঔপনিবেশিক শাসনদন্ডে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে. . .তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও তাগিদে পাশ্চাত্য ইতিহাস চেতনাকে তথাকথিত ‘লিবারাল আদর্শ’ এর অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশের ঐতিহাসিকরাও ইউরোপীয় ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস লিখনের অনুসরণ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। ফলে ইতিহাস চর্চায় এই জাতীয় সার্জারিতে সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর ভূমিকা মারাত্বকভাবে অবহেলিত হয়।তাঁর মতে, রাজনীতিতে প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী শ্রেণী হল নিম্নবর্গ, কিন্তু উচ্চবর্গের মানুষ এযাবৎকাল ইতিহাস লিখেছেন, এবং ইতিহাসের রসদ তাঁরাই জুগিয়েছেন। ফলে উচ্চবর্গের ইতিহাস হয়ে উঠেছে জাতীয় ইতিহাস চর্চার বিশেষ নমুনা, যেখানে নিম্নবর্গের ইতিহাস উপেক্ষিত হয়ে এই প্রয়াস একটি অলিখিত আদিকল্পের জন্ম দিয়েছে। গুহর মতো তুখোড় ইতিহাসবেত্তারা তথাকথিত এই জাতীয় ভাবনার মিথ ভেঙে ইতিহাস চর্চার নবায়ন ঘটিয়েছেন সাবলটার্ন স্টাডিজের মধ্য দিয়ে। নিপীড়িতের ইতিহাস, সাহিত্যের উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ, অথবা রাজনীতি, নৃতত্ত্ব, শিল্পের ইতিহাস বা সংস্কৃতিপাঠ—সবেতেই এই ‘মানবচেতনা’র আবিষ্কার করেছেন রণজিৎ গুহ। তাঁর মতে ক্ষমতা বৃত্তের বাইরে থাকা শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী, নিম্নবর্ণ, মহিলা শ্রেণীর ভূমিকা বা অবদানের উল্লেখ যথাযোগ্য ভাবে নির্মিত হয়নি। এই প্রথাগত ইতিহাস চর্চার গতিধারা বদলে দিয়েছেন ।
যদিও সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গের মানুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেনি। কিন্তু রাওলাট সত্যাগ্রহ ( ১৯১৯ ) বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা প্রাধান্য অস্বীকার করার জায়গা নেই। জনগণের বেশিরভাগ ছিল নিম্নবর্গের মানুষ, তাদের বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা হলে সে ইতিহাস অবশ্যই অসম্পূর্ণ থাকে। অধ্যাপক গুহ উচ্চবর্গের মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিদেশি শাসক , বণিক , পুঁজিপতি , দেশি অভিজাত , বণিক , বুর্জোয়া ও উচ্চস্তরের মানুষদের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্ক হল শোষক ও শোষিতের। উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দরিদ্র মানুষের মজুরি, খাজনা, ঋণ, দারিদ্র্য , দুর্ভিক্ষ, বেকারি, জমি হারানো, ফসলের নায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া বা কৃষকের শোষণ, বঞ্চনা, প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার ভাবনা বিশ্লেষণ করার কারিগর ছিলেন ঐতিহাসিক গুহ। এক ধাপ এগিয়ে তিনি কৃষক চৈতন্যের স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের জীবনযাত্রা, উপকথা, পুরাণ, জনশ্রুতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারকে ইতিহাস নির্মানের উপাদান হিসেবে উপেক্ষা না করে বরং ‘তল থেকে দেখার’ অভিপ্রায় যুগিয়েছেন।
ইতিহাসকে প্রথাগত ছকের বাইরে থেকে বিচার করার নিরন্তর যাত্রাপথে তিনি বিশ্বময় খ্যাতিমান ঐতিহাসিকদের এক ছত্রেতলে আনতে সক্ষম হন। এডওয়ার্ড সাঈদ জানিয়েছেন যে ভারতের সরকারি ইতিহাসে যা নেই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তা জুগিয়ে ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন।এখানেই তাঁর স্বার্থকতা। সম্ভবত এই জন্য অমর্ত্য সেন তাঁকে বিশ শতকের সবচেয়ে সৃজনশীল ভারতীয় ঐতিহাসিক বলে মনে করতেন।
রণজিৎ গুহ ১৯২৩ সালের ২৩ মে, বরিশালের বাখরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে তালুকদার ভূস্বামী পরিবারে জন্ম৷ ঔপনিবেশিক ভূমি বন্দোবস্তের পথ ধরে ‘রাজা – প্রজার’ শ্রেণি-পরিচিতির গ্লানি তাঁর মনকে শৈশবেই ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছিল। অনেকেই মনে করেছেন এই ধাক্কা পরবর্তী জীবনে তাঁকে নতুন ইতিহাস-ভাবনার উন্মেষ নির্মাণে সহায়তা করে। পড়াশুনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় পাড়ি দেন, ভর্তি হন মিত্র ইনস্টিটিউশন, অতপর প্রেসিডেন্সি কলেজে। পিতা ছিলেন হাইকোর্টের আইনজীবী। ছাত্র জীবনেই জড়িয়ে পড়েন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। সিপিআই-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে যুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরে প্যারিসে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনেও যোগ দেন। দলের প্রতিনিধি হিসেবে সাইবেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও চিন বিপ্লব সরজমিনে ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ১৯৫৬ সালে, দেশে ফেরার কিছু পর, হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত অনুপ্রেবেশের বিরোধিতায় তিনি দল ছেড়ে দেন।
দল ছাড়ার পর তিনি বিদ্যাসাগর কলেজ ও সুশোভন সরকারের আমন্ত্রণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাল পড়ান। কিন্তু এখানেও তাঁর শত্রুর অভাব হয়নি। অবশেষে ১৯৫৯ সালে তিনি দেশ ছেড়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান, এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে রিডার পদে যোগ দেন। পরে অবশ্য নব্বই দশকের আগেই তিনি নৃতত্ত্ব পড়াতে ক্যানবেরায় কাটিয়েছেন কিছুকাল। প্রাতিষ্ঠানিক কোলাহল থেকে প্রায়-অন্তরিন অবস্থায় ষাটের দশকে বিলেতে কিছু পাঠচক্র চালিয়েছিলেন ।গাঁধী নিয়ে ভাবতে চাইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।
১৯৮০ সালে তিনি সাবঅলটার্নএর ভাবনা গুলি অক্সফোর্ড প্রকাশও করতে থাকেন। একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনায়, সেন্টার ফর স্টাডিজে, এক্ষণ সাময়িকপত্রে গুরুত্ব পেতে থাকলো তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা কর্মগুলি। তাঁর মতে, ভারতীয় ইতিহাস-লিখন এক বদ্ধতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারন উচ্চবর্গকে স্বতঃসিদ্ধভাবে আলোচনার মেইন স্ট্রিম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তথাকথিত এই ভাবনার শিকল ভেঙ্গে নিম্নবর্গের নতুন এই ইতিহাসকে সর্বস্তরের মানুষের দরবারে হাজির করেন । তাঁর মতে ব্যক্তিক চৈতন্য, বিদ্রোহী মানস ও আদিসত্তার প্রকরণগুলি আলোকপর্বের গোঁড়ামো কাটিয়ে ইতিহাসবিদকে নতুন করে ভাবতে হবে,পড়তে হবে ৷
রণজিৎ গুহ ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দয়া: রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা (২০১০), প্রেম না প্রতারণা (২০১৩) ইত্যাদি। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এসেছে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, যেমন; কবির নাম ও সর্বনাম (২০০৯), ছয় ঋতুর গান (২০০৯) প্রভৃতি। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ,রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই তাঁর ভাবনায় ঠাঁই পেয়েছিল।
নব্বই দশকে বাংলা ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, ভাষাদর্শন ,জীবনানন্দ, সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ আরও বহুবিধ ভাবনার সমষ্টি থেকে দূরে থাকতে পারেননি তিনি।
ভাবনার ইতিহাস, কখনও সাহিত্য, বা দর্শনে বুঁদ হয়ে থেকেছেন তিনি। তাঁর এই মানবিক প্রয়াস বা বৌদ্ধিক চর্চা নতুন সভ্যতা, ভারতবর্ষকে একান্ত নিবিড় করে দেখার সুযোগ করে দেয়। তিনি সাহিত্যকে ইতিহাস, রাজনীতি এবং শেষপর্যন্ত প্রজ্ঞাময় দর্শন হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছেন আমাদের।