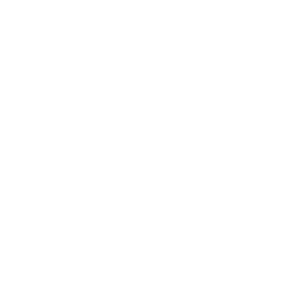শব্দের স্বরূপ, উদ্ভব, বিকাশ যেদিক থেকেই আলোচনা করা যাক, শব্দ সব সময় সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ। তাকে সম্প্রদায়ের রঙে রাঙিয়ে তোলা হয় মাত্র। ঐতিহাসিক কারণে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই তা ধর্মীয় চরিত্র পরিগ্রহ করে। আসলে কোনও শব্দেরই ধর্মীয় কোনও রূপ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ‘পানি’ শব্দের কথাই ধরা যাক। এটা আরবী নয়, ইসলামীও নয়। তেমনি ইসলাম-বিরোধী বা হিন্দুয়ানীও নয়। কিন্তু ধর্মীয় রূপ না থাকলেও সব ভাষাতেই অনেক শব্দেরই একটি কৃষ্টিগত রুপ থাকে।
পানি বাংলাভাষী বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা। ঘটনাচক্রে তাদের বেশীরভাগই মুসলমান। কিন্তু বেশীরভাগ বাঙালি হিন্দু ছাড়া ভারতের প্রায় সব মানুষই পানি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। অবশ্য সাঁওতালরা পানি বা জলকে নিজ ভাষায় ‘দাঃ’ বলে থাকেন, তেলেগু ভাষায় ‘নীলু’ বলা হয়। কানাড়ি, মালয়ালম, তামিল ইত্যাদি ভাষায় পানি বলা হয় না। কোথাও “নীরু’ ভেল্লম ইত্যাদি বলা হয়। তবে অসমীয়া, উড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, ভোজপুরি, হিন্দি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, কাশ্মীরি, মৈথিলী, পোছ, নেপালী ইত্যাদি সমস্ত ভাষাতেই পানি শব্দ কথ্য ও লেখ্যরূপে – ভারতীয় সাহিত্য-কারো ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
পানির ভারতীয়তার ওপর আরও খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। ভারতে মুসলিম অভিযানের বহু পূর্বের ইতিহাস গুপ্তযুগের কথা। প্রতাপশালী গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের মধ্যে বরাহ ও তার পুত্র মিহির ছিলেন অন্যতম। মিহিরের পত্নী ওগবতী খনা। খনার পান্ডিয়া আজও লোকের মুখে মুখে। বাংলা সাহিত্যের এবং ভারতীয় কৃষি ও গৃহ-বিজ্ঞানের মূল্যবান সম্পদরূপে খনার বচনগুলি যেমন শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে, তেমনি হিন্দুদের আচারে-বিচারে ও দৈনন্দিন জীবন ধারার নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আসছে। কৃষি-সংক্রান্ত খনার বচনগুলির মধ্যে আমরা পানি ব্যবহারের সন্ধান পেয়েছি। ‘কৃষিগাথা’ নামক পুরনো বই থেকে আমরা এই সন্ধান উদ্ধার করছি—”চাঁদের সতার মধ্যে তারা/ বর্ষে পাণি মুষলধারা।”।
উল্লেখ্য, সমালোচকদের দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গুপ্তযুগের ইতিহাসের আলোকে খনা হচ্ছে প্রীতিময় প্রারম্ভিক কালের মহিলা। তাছাড়া পানি শব্দ বাংলার আদিগ্রন্থ চর্যাপদে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আগে বৈদিক সংস্কৃতে ‘পানি’ (প্রাচীন বানান পাণী) অর্থে ‘অপ’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহাত হয়েছে, জল ব্যবহৃত হয়নি। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মমত ও নাথপন্থীমত খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দী কি তারও পূর্বে চলিত ছিল। সহজিয়া নাথপন্থী মত প্রচারী একটি হেঁয়ালি চর্যার রেখাচিত্র উদ্ধার করেছেন সুকুমার সেন তার ‘প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী”-তে (বিশ্বভারতী)। তাতে আমরা ‘পাণী’র রূপ দেখতে পাই। হু-বহু চর্যা-চিত্রটি তুলে ধরলাম—“গঙ্গা যমুনা মাঝেরে বহই নাই/তহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইয়া লীলে পার করেই/ বাহু তু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা/ সদগুরু-পাঅপসা ঐ যাইব পুনু জিনউরা।/পাঞ্চ কেড়ায়াল পড়ন্তে মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী/ গঅন -দুখোলো সিঞ্চহুঁ পাণী পই সই সান্ধী।” রামাই পণ্ডিত তার শূণ্যপুরাণে (একদশ দশকে) লিখলেন— “পুমরি কাঁপা এ লইব ভূম খানি/আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পাণী”। প্রাচীন লোকসাহিত্য লোক গাথা, ছড়া, শিব-চণ্ডীর পাঁচালি ইত্যাদিতেও পানি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়—“পশু দিবা লাল বড়িটা কাজী দিয়া গুইলা/ তশ্যু দিবা নীল বাড়টা কুয়ার পাণি তুইলা। “
আমরা আরও কিছু তথ্য তুলে ধরতে পারি কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র স্বামী অভেদানন্দের “বিশ্ববাণী” পত্রিকা থেকে। রতিশরঞ্জন শর্মার সহায়তায় ব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্যগীত সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের কৃষ্টি বৃদ্ধি করেছেন। সাহিত্যের অঙ্গে এটি যেন একটা গীতালি। এই মেয়েলি গান-গুচ্ছের মধ্যে আমরা বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ‘চুলপানি’, ‘ঘটপানি’, ‘ঘিলাপানি’, ‘তৈলপানি’ ইত্যাদির চেহারা দেখতে পাই। (শারদীয় বিশ্ববাণী, ১৩৭৪)।
মাঘমণ্ডল ব্রত হিন্দু নারীর রঙ। প্রাচীনকাল থেকে ফেলে আসা এই শীতকালীন এত দ্বারা হিন্দুর কুমারী মেয়েরা সূর্যদেবের পূজা করে। এই লোকব্রত ছড়ার মধ্যে ‘পানী’ প্রচলিত রয়েছে। হারাধন দত্ত ‘মঙ্গলকাব্য, গ্রাম্য ছড়া ও ব্রতকথা’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে আমরা পানির সন্ধান পেয়েছি, যার উদ্ধৃতি নিচে দিলাম— “ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ওঠে পানি।/ ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি মায়ের কান্দন শুনি।” হারাধন বাবুর সংগৃহীত মেয়েলি ব্রত ছড়ার মধ্যে যে কামনা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে তাতেও আমরা পানি-র খোঁজ পাই—’আমি যেন হই রাজার বউ।/কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি/আমি যেন হই রাজার রাণী ।” (বিশ্ববাণী, চৈত্র ১৩৭৪)।
‘রাঢ়ের ধর্মপূজা’ নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. অমলেন্দু মিত্র। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বীরভূম বিবরণী’-র ২য় খণ্ডের ৫০৯ পৃষ্ঠায় শিবপূজার বাণব্রত উৎসব সম্পর্কে অমলেন্দু বাবু বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এই বর্ণনামতে বীরভূমের পাইকোড় গ্রামে অনুষ্ঠিত বাণব্রতে নদীস্নানকালীন যে ‘ঘাটশুদ্ধি মন্ত্র আমরা পাই— তাতে ‘পানি’ শব্দের উল্লেখ আছে—“ঘাট ঘাট মহাঘাট, সোনা আর রূপোর পাট / হনুমান সৃজিল ঘাট, সিঞ্চিলে পঞ্চম পানি।”
ষোল শতকের গৌড়বঙ্গে মঙ্গলকাব্যের বান ডেকেছিল। সেগুলি রচিত হয়েছিল রাঢ়বঙ্গের বাংলা ভাষায়। সে যুগের কাব্য কৌশলের কবীন্দ্র ছিলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। কবিকঙ্কন উপাধিপ্রাপ্ত এই কবি ছিলেন বর্ধমান-মেদিনীপুর মৃৎ খণ্ডের খাস বাঙালি। তিনি রচনা করে গেছেন ‘অভয়ামঙ্গল’ বা ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্য। আমাদের নিরীক্ষণ মতে, তিনি তাঁর এই বিখ্যাত কাব্যে অত্যন্ত অসঙ্কোচে অন্তত ৪০ চল্লিশ জায়গায় ‘পানী’ শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, এবং সে ব্যবহার আজকের সাহিত্যিক বিচারেও স্থানসঙ্গত ও অর্থসঙ্গত। শব্দকোষকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে পানি শব্দের ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে প্রাচীন ও নবীন বাংলা সাহিত্য কর্মের নামিদামি কর্ম থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন— ‘তীর্থ বারনসীর পানি’ (শূন্য পুরাণ)/ ‘পাণী’- (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরখণ্ড)/ ‘জোয়ারের পাণি, নারীর যৌবন’- (চণ্ডীদাস)/ ‘যেন মেঘে মেঘে পাণী পসালা’–(কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম)। ‘চলে বহে পাণি’—- (কাশীদাসী মহাভারত)/ ‘যৌবন রাধে পাণির ফোটা’- (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)/ ‘আহার পাণি নিদ্রা রহিত’।
( বাঙালির প্রতিদিনের জীবনের কথ্যভাষায় বহু শব্দে, প্রবচানে পানি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যা যেমন—পানিফল, পানিকৌড়ি, জলপানি, পানিবসন্ত, পানিশঙ্খ, পানিকাক, কালাপানি, পানিসার, পানিশিট পানিকচু, পানিডুবুরি, পাণিগ্রহণ, পানকৃত, পানপড়া, পানমশলা, পানসে, পাস্তা, প্রভৃতি। স্থান নামে পানিহা পানিতর, ইত্যাদি। প্রবাদ প্রবচনে ‘ধরি মাছ না ছুই পানি’, ‘মেঘ চাইতে পানি, খোদার মেহেরবানি’ ইত্যাি আরও রয়েছে—’পানি পানি মুখ’ (বিবর্ণ-ফ্যাকাশে), ‘বিষ পাণি হওয়া’, ‘আগুনে পানিপড়ী’ প্রভৃতি।
‘পানি’র পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ‘জল’ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। পানির মত জল ও বাংল শব্দভান্ডারের বহু শব্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্তমান। যেমন— জলসার, জলচর, জলসত্র জলপাণি, জলকর, জলপ্রপাত, জলযোগ, জলযান, জলবায়ু, জলমগ্ন, জলাশয়, জলাতঙ্ক, জলাঞ্জলি, জলো, জলসম, ইত্যাদি।
যাই হোক, সংস্কৃত থেকে জাত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও কথ্য স্তরে পানি শব্দ একসময়ে সার্বজনীনভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এটাও বোধ হয় জানা যে, ‘জল’ যেমন সংস্কৃত উৎসের, তৎসম শব্দ: ‘পানি’-ও তেমনি সংস্কৃত উৎসের, তবে তদভব। ‘পানীয়’ থেকে পানি। তা না জেনেই এক শ্রেণীর হিন্দু বাঙালি ‘পানি’-র উপর বিদ্বেষ নিয়ে বসে থাকেন। ‘যবন’ স্পর্শদোষে পানিকে যেন কুল হারাতে হল। কিন্তু অভিধানে যখন এই বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পাই তখন দুঃখ হয় বৈকি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বেশীরভাগ হিন্দু অভিধান-প্রণেতার অভিধানেই জল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘বারি’ ‘সলিল’ ইত্যাদি শব্দের দেখা পাওয়া গেলেও ‘পানি’ কথাটির দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে। এটা অচেতন নয়, সচেতন বর্জন- এটাই বিপদের কারণ। মুসলিম শাসকরা চৌদ্দঘাটের পানি পান করে বাংলায় এসেছিলেন। তাই তাদের উত্তরসূরীরাও পানি দখল করলেন আর সেই দুঃখে হিন্দুরা পানি ছেড়ে জল ধরলেন।
‘দেশ’-এর এক পত্রলেখক জন্মজিত রায় বাংলা ভাষায় জল শব্দের ব্যাপক প্রচলনের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, “আধুনিক বাংলায় ‘পানি’ শব্দ বন্ধ হওয়ার কারণ রেনেসাঁস বাংলায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসুদনের হাতে বাংলা ভাষায় Standardisation। অবশ্য এরও আগে চৈতন্যযুগেই এটা হতে শুরু করেছে তৎসম শব্দ ব্যবহারের জন্য। নবযুগের বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন ও সাহিত্যিক রূপ দান করতে গিয়ে বাংলা ভাষার স্থপতিবৃন্দ অনিবার্যবশত ‘তৎসম’ বা সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। … দ্বিতীয় কথা, বাংলা ভাষা রেনেসাঁসি যুগে তৎসম শব্দ দিয়ে সমৃদ্ধ হতে গিয়ে অনেকগুলি দেশজ ও তদভব শব্দকে বর্জন করেছে। ‘পানি’ এরকম একটি শব্দ।” (দেশ, ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৪)।
কিন্তু বিষয়টি যে এত সরল নয় তা বলা বাংলা। বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রে পানি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে জলে উত্তরিত হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। কিন্তু কেন সংস্কৃত শব্দ পানি থেকে বাঙালি হিন্দুর এই মুখ ফিরিয়ে নেবার প্রবণতা। এর সুত্রপাত ভর ও সেন যুগ থেকে। এই যুগে নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গৌড়-বঙ্গের স্থানীয় সংখ্যাগুরু পরাজিত বৌদ্ধদের প্রতি শুরু হল প্রবল বিষেষভাব, ঘৃণা আর তার সাথে যুক্ত হল বৌদ্ধদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সচেতন ব্রাহ্মণ্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটল পার্থক্য নির্ণয়কারী বিশেষ বিশেষ শব্দ গ্রহণ-বর্জনে, বাংলায় সংস্কৃত থেকে জন্ম প্রাকৃত ভাষায় নতুন করে সংস্কৃতরূপ প্রকরণে এবং বিশেষ বিশেষ আচরণে। এই পর্যায়েই ব্রাহ্মণ ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ‘পানি’ ছেড়ে ‘জল’ বলার প্রবণতা শুরু হয়।
পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে নিগৃহীত ও অপমানিত বৌদ্ধরা তুর্কি ও আফগান শাসনকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে আহত ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বের দৃশ্যতার নব মুসলিমদের প্রতি আরও বেড়ে গেল আর সেই অনুপাতে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে পানি ছেড়ে জল বলার প্রবণতা বেড়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদী শুর ও সেন যুগে যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল, তুর্কি-আফগান যুগে তা গতিপ্রাপ্ত হয়ে কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র ‘পানি’ শব্দ থেকে যুগপৎভাবে আসামাধিভাগে জল-পানির ব্যবহারে এসে পৌঁছাল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতে, এ সময়কার সমস্ত সাহিত্য কর্মে তাই জল-পানির যুগপৎ অবস্থান।
ইংরেজ আমলে এসে ইংরেজ অনুসৃত ভেদনীতির দরুণ এ প্রবণতার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটল। ঈশ্বর গুপ্তে এসে বাঙালি হিন্দুর শব্দভান্ডারে জল শব্দ প্রায় সার্বজনীনতা পেল। দ্বিধা বিভক্ত বাঙালি সমাজের অবশিষ্ট নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বের প্রভাবে পানির বদলে জল শব্দকে গ্রহণ করে নিল। যদিও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালি হিন্দুরা (বিশেষত নিম্নবর্ণের) পানিই বলতে থাকল।
এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলায় যে সমস্ত অঞ্চলে নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সেই সমস্ত অঞ্চলে আদি বাঙালি সমাজের রীতিনীতি চালচলন আজও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান আছে আর এই সমস্ত অঞ্চলের (যেমন শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম) বাঙালি হিন্দুরা আজও পানি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও সম্ভবত শেষবারের মত পানি শব্দের প্রয়োগ করলেন দীনেশচন্দ্র সেন ‘বৃহৎ বঙ্গ’ গ্রন্থে (১খন্ড, পৃ. ৫৯১)। আসলে “বৌদ্ধগণ মুণ্ডিত মস্তক ছিলেন, এ জন্যই তাঁহারা উত্তরকালে হিন্দুগণ কর্তৃক ‘নেড়া’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের অনেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উক্তনামে বঙ্গীয় মুসলমানগণও পরিচিত হইয়া থাকেন।” আর নেড়া বা নেড়ে বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হওয়া মানুষের শব্দাবলীতে পানি শব্দই থেকে গেল।
‘পানি’ থেকে ‘জল’-এ উত্তরণের ইতিহাস এটাই।